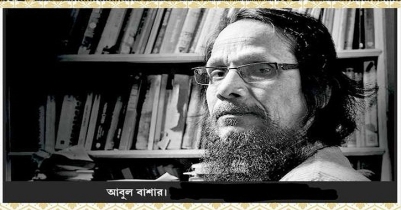সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
সমাজ সমাজের মতো চলবে এটাই স্বাভাবিক, যদি না বাধা দেওয়া হয়। বাধাটা তাঁরাই দেন সমাজকে যাঁরা বদলাতে চান। তাঁদের উপলব্ধি থাকে এমনটা যে সমাজ মোটেই ঠিক নেই, তার ভেতরে অন্যায় রয়েছে; এভাবে চললে মানুষের মঙ্গল হবে না; সমাজকে তাই বদলানো চাই। তা অন্যায়টা কোথায়? সমাজ-পরিবর্তনকামীরা বলবেন মূল অন্যায়টা বৈষম্যে। সমাজে যত উন্নতি ঘটবে ততই বৈষম্য বাড়বে। উন্নতির এই ধারাটা পুঁজিবাদী। একে যাঁরা বদলাতে চান তাঁরা সমাজতন্ত্রী।
আমাদের সমাজে সামন্তবাদিতা ছিল, এখন চলে এসেছে সে পুঁজিবাদে। বৈষম্য সামন্তবাদেও ছিল, পুঁজিবাদে পৌঁছে তা আরও ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করেছে। এই বাস্তবতাটা সামাজিক ইতিহাসের যে কোনো বইতেই পাবার কথা। পাওয়া যাবে আত্মজৈবনিক রচনাতেও, যেমনটা পাবো আমরা অলকনন্দা প্যাটেল লিখিত স্মৃতিকথায়। তাঁর বইটির নাম পৃথিবীর পথে হেঁটে (ঢাকা, ২০১৭)। সুলিখিত এই বইটি উপন্যাসিক কৌতূহলের সঙ্গে পড়বার মতো, আবার এর কাহিনী ও ঘটনাবলী যে সামাজিক ইতিহাসের সন্ধান দেয় তাতে আমাদের সমাজের বৈষম্যমূলক অগ্রগমনের ধারণাটা পুরোপুরি সমর্থিত হয়।
অলকনন্দা ঢাকার মেয়ে, জন্ম ১৯৩৭ সালে, ঢাকার গেন্ডারিয়াতে। ঢাকায় তাঁর মায়ের বাড়ি, বাবার বাড়ি বরিশালে। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন গৈলা, গেন্ডারিয়ার পূর্বপুরুষদের স্মৃতির উদ্দেশে। শিরোনাম ইঙ্গিত দিচ্ছে তিনি পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরেছেন। বইয়ের ভেতরে সে-কাহিনীটা রয়েছে, নয় বছর বয়সে তিনি চলে যান শান্তিনিকেতনে, তারপরে তাঁর পড়াশোনা কাশীতে ও যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ডে। অধ্যাপনা করেছেন দিল্লি ও লন্ডনে; গবেষণা করেছেন ইতালিতে। তাঁর নিজের অধ্যয়নের এলাকা অর্থনীতি; তাঁর পিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রথমে খ্যাতিবান ছাত্র ও পরে যশস্বী অধ্যাপক, নাম অমিয় কুমার দাশগুপ্ত। অলকনন্দা বিয়ে করেছেন একজন অবাঙালিকে, তাঁর স্বামী আই জে প্যাটেল ছিলেন এক সময়ে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার গভর্নর, পরে লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্সের ডিরেক্টর। ১৯৪৬-এ পিতামাতার সাথে দেশ ছেড়েছেন, আর ফেরা হয়নি। কিন্তু দেশের স্মৃতিতে এবং আত্মীয়স্বজনের সান্নিধ্যে নিজেকে সমৃদ্ধ করে রেখেছেন, সর্বদা। বইটি লিখেছেন নিজের সজীব স্মৃতিশক্তির ওপর ভর করেই যে শুধু তা নয়, গবেষণা, সাক্ষাৎকার, আলাপ-আলোচনা, অন্যের লেখা বইপত্রের সাহায্য নিয়েও। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চিঠিপত্রের ব্যবহার। চিঠি লেখা জিনিসটা তো এখন প্রায় উঠেই গেছে; লোকে মোবাইলে, ফেসবুকে, ইন্টারনেটে যোগাযোগ করে; তাতে সুবিধা আছে, কিন্তু ইতিমধ্যে বড় রকমের একটা লোকসান ঘটে গেছে, সেটা হলো মনের ভাব গুছিয়ে প্রকাশ করার এবং সামাজিক ইতিহাসের উপাদান জমা রাখার অভ্যাসে ঘাটতি। আমার পিতা বলতেন একবার লেখা দশবার পড়ার সমান; সে-কথাটাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না।
অলকনন্দার পিতা অমিয়কুমার দাশগুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এসেছেন ১৯২২ সালে। এম এ পাস করেছেন ১৯২৬-এ। সেই বছরই লেকচারার হয়েছিছেন। ২৪ বছর কাটিয়েছেন তিনি ঢাকা শহরে, মাঝখানে দু’বছর ছিলেন লন্ডনে, উচ্চশিক্ষার জন্য। শিক্ষক হিসেবে ছিলেন অসাধারণ; তাত্ত্বিক অর্থনীতির গবেষক হিসেবে ছিলেন যশস্বী। কিন্তু পরিবারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। লেকচারারদের আয় ছিল সীমিত, ভাড়া বাসায় থাকতে হতো, অমিয় দাশগুপ্তকে আবার নিয়মিতই অর্থ সাহায্য করতে হতো তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিবারকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আত্মত্যাগ করেছিলেন, নিজে কষ্ট সহ্য করে খরচ জুগিয়েছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার পড়াশোনার। ভ্রাতার আনুকূল্যের কারণেই অমিয় দাশগুপ্ত ঢাকায় এসেছিলেন, পড়তে। কলকাতাতে যাওয়াটা কঠিন ছিল। ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, সেটাই ছিল ভরসা। শিক্ষার অগ্রগতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকাটা বেশ বড়; শিক্ষার সে সুযোগ করে দিয়েছে অনেকের জন্য। সেই সঙ্গে আরও জরুরি একটা কাজ করেছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়, সেটি হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশকে সহায়তাদান। মুসলিম মধ্যবিত্ত তো অবশ্যই, হিন্দু মধ্যবিত্তও সহায়তা পেয়েছে, যদিও নানান ঐতিহাসিক কারণে মুসলমানদের তুলনায় তারা অন্তত পঞ্চাশ বছর এগিয়ে ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রত্যক্ষ ফল। কেবল বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে ঢাকায় অনেক দালানকোঠাও উঠেছিল, ঠিকাদারী করে লোকের হাতে নগদ পয়সা এসেছিল, চাকরি বাকরিতেও কিছুটা সুবিধা হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গটা টেকেনি; ভঙ্গবঙ্গ আবার জোড়া লেগেছে। কিন্তু ফাটলটা রয়ে গেছে। সেটা হলো হিন্দু-মুসলমান বিরোধ। ইংরেজরা উস্কানি দিয়েছে; কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত সুযোগসুবিধার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে যে লড়াই বাধিয়েছে সেটাও খুবই সত্য। ফলে ১৯৪৭-এ আবার ভাগ হলো। এবার প্রদেশ ভাগ নয়, দেশ ভাগ; যেটা ১৭৫৭-এর পরে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। একটা প্রশ্ন থাকে, ১৯০৫-এর প্রশাসনিক বঙ্গভঙ্গ যদি রদ না হতো তাহলে কি ১৯৪৭-এর ট্র্যাজেডিটাকে ঠেকানো যেতো? হয়তো যেতো। বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল এটাই বাস্তবতা। ভাঙবার উদ্যোগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের আবেগ প্রবল হয়ে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধ লকলক করে বেড়ে উঠে জাতীয়তাবাদকে যে ঠেলে দিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ গলির ভেতরে সেটাও সত্য। জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা সেজে তা-ব করেছে, যার বোঝা বহন করেছে এদেশের মানুষ।
অলকনন্দার শৈশবের বছরগুলোর বেশির ভাগ কেটেছে পুরানা পল্টনে। পুরানা পল্টন তখন নতুন একটা আবাসিক এলাকা। কোথাও দালান, কোথাও টিনের ঘর। অনেক বাড়িতেই বিদ্যুৎ ছিল না। বৃষ্টি হলে পানি জমে যেত রাস্তায়। সাহিত্যে, বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসুর লেখাতে পুরানা পল্টনকে ভারি রোমান্টিক মনে হয়। টিনের চালের দুঃসহ তাপ-যন্ত্রণা ঢাকা পড়ে যায় বৃষ্টির রিমঝিম আওয়াজের মাধুর্যে। তা বুদ্ধদেব বসুদের কথা অবশ্যই স্বতন্ত্র, তাঁরা কল্পনার জগৎটাকে বড় করে তুলবার অসাধারণ ক্ষমতা রাখতেন। অলকনন্দার বইতেই তো একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। যমুনা নদীর ধারে এক সন্ধ্যায় বন্ধুরা গল্প করছিলেন। দলে ছিলেন পরিমল রায়, অর্থনীতির ছাত্র। বুদ্ধদেব বসু হঠাৎ বলে ওঠেন, ‘পরিমল, দেখ দেখ হরিণটা কেমন হেঁটে যাচ্ছে।’ পরিমল রায় বলেছিলেন আসল কথাটা; ‘ওটা হরিণ নয়, বাছুর।’ হরিণে-বাছুরে বিস্তর ব্যবধান, কিন্তু বাছুরকেও হরিণ মনে করা সম্ভব, যদি দেখবার চোখ থাকে।
দেখবার ওই চোখ না থাকলে মনে হবে বড়ই সামান্য ছিল ঢাকা শহর। এ শহর বায়ান্ন বাজারের, তেপ্পান্ন গলির। নবীন সেন একবার এখানে এসেছিলেন, ভীষণ বিতৃষ্ণা জন্মেছিল তাঁর শহরটিকে দেখে। বঙ্কিমচন্দ্র তো বলেছেনই ঢাকায় গেলে প্রচুর কাক, উকিল ও মুসলমান দেখা পাওয়া যায়; তিন প্রাণিই কলহপ্রিয়। এই শহর বৈরী ছিল মেয়েদের জন্য। অলকনন্দা জানাচ্ছেন যে ছেলেদের জন্য তবু সুযোগ ছিল বাইরে গিয়ে খেলাধুলার, সাইকেলে চড়ে ঘোরাফেরার, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশার; মেয়েরা ছিল পাড়াবন্দি। আশেপাশে কোনো স্কুল নেই দেখে অলকনন্দার বাবা-মা দাশগুপ্ত একাডেমী নামে একটি স্কুল খুলেছিলেন। নিজেদের বাসার ভেতরেই। ছাত্রী ওই একজনই। শিশু অলকনন্দা। তার পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্রও তৈরি করা হতো। ভাইভা পরীক্ষার জন্য এক্সটার্নাল পর্যন্ত আসতেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি সরকারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন; কিন্তু যাতায়াতের ব্যাপারে অসুবিধা ছিল। তাকে তাই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল শান্তিনিকেতনে, নয় বছর বয়সে। পাড়ার ছোট পরিসরে নাটক ও গানের অনুষ্ঠান হতো। মেয়েরা অভিনয় ও আবৃত্তি করতো, গান গাইতো একসাথে ও একক কণ্ঠে; কিন্তু নৃত্যের অনুমোদন ছিল না। জগন্নাথ হলের মঞ্চে একবার একটি ছোট্ট মেয়ে তার বোনের-গাওয়া গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৃত্যের মতো কিছু অঙ্গভঙ্গি করেছিল, তাতেই রক্ষণশীল ঢাকার মুখপত্র সাপ্তাহিক চাবুক পত্রিকা বড় বড় অক্ষরে খবরের শিরোনাম করেছিল, জগন্নাথ হলে আবার মেয়ে নাচিল।
অলকনন্দার বই বলছে মহিলারা তখন বাইরে যেতেন না, তাঁরা সদরঘাট দেখেননি, তাঁদের দৌড় ছিল ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয় ও বাটার জুতার দোকান পর্যন্ত। যাতায়াতে বিঘœ ছিল। ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করতে হতো। পথে ছিনতাইয়ের ভয় থাকতো। অলকনন্দার মায়ের গলা থেকে একবার সোনার চেন ধরে টান দিয়েছিল এক ছিনতাইকারী। সবটা নিতে পারেনি, অর্ধেকটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। চোরটি পরে ধরা পড়েছে। আদালতে বিচার বসেছে। শাস্তি হয়েছে। এটা তখনকার দিনের কথা; গত আট দশকে ঢাকার উন্নতি আকাশ মাটি উভয়কেই কাঁপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে পুরানা পল্টনের খবর কি? লেখিকা চল্লিশ দশকের পুরানা পল্টনকে খুঁজতে বের হয়েছিলেন, গিয়ে দেখেন পুরানা পল্টন আর নাই, উধাও হয়ে গেছে। আমরাও সেটা জানি। জানি যে বৃষ্টি হলে সেখানে কেমন দুঃসহ জলবদ্ধতা তৈরি হয়। আগের দিনে তবু মেয়েদের বেলাতে না থাকলেও ছেলেদের বেলাতে চলাফেরার সুযোগ ছিল, এখন পায়ে পায়ে বাধা। হাঁটার উপায় নেই। গাড়ি অচলমান অবস্থায় বসে থাকে, রিক্সা উল্টে পড়ে যায় গর্তে। ছিনতাইকারীরা ছুরি, পিস্তল ইত্যাদি নিয়ে অপেক্ষমাণ থাকে যত্রতত্র। তখন তবু খেলার জন্য মাঠ ছিল, খেলার মাঠ এখন সুখস্বপ্ন। শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়াই কঠিন।
এই হচ্ছে উন্নতির চরিত্র। একেই বলে পুঁজিবাদী উন্নতি। আর মেয়েদের চলাফেরা? জরীপ বলছে নারীর প্রতি সহিংসতার দিক থেকে ঢাকা শহর এখন পৃথিবীর নিকৃষ্টতম শহরগুলোর একটি। চ্যাম্পিয়ান না হলেও কাছাকাছি। চতুর্থ স্থানের অধিকারী। আরও উপরে ওঠার তালে আছে। এখন আর গলার হার নয়, মেয়েরাই স্বশরীরে ছিনতাই হয়ে যায়। আদালতপাড়াতেও শিশু ধর্ষণ চলে। ওকাজ পুলিশের লোকেও করে থাকে। ছিনতাইয়ে চোর-ডাকাতরা শুধু নয় আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর লোকেরাও হাত লাগিয়েছে। মেয়েরা খুন হচ্ছে গৃহে, হোটেলে, পথেঘাটে, গণপরিবহনে। ধর্ষণ চলছে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেও। সরকারি দলের এক ছাত্রনেতা নিজের বাহাদুরী জারি করে ধর্ষণের ক্ষেত্রে সেঞ্চুরি করবে বলে একবার ঘোষণা দিয়েছিল। সদম্ভে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতে উৎসবে যোগ দিতে এলে মেয়েরা লাঞ্ছিত হয়। বইমেলাতে জঙ্গিরা হত্যা করে প্রগতিশীল লেখক ও প্রকাশককে। গুম ও খুন এখন রোজদিনের স্বাভাবিক ঘটনা।
হিসাবে দেখছি বয়সে অলকনন্দা আমার চেয়ে এক বছরের ছোট। ঢাকা ছেড়ে ওঁরা চলে গেছেন সাতচল্লিশের আগেই, আমরা এসেছি সাতচল্লিশের শেষ দিকে। ঢাকা তখন খুবই ম্রিয়মান এক শহর। কলকাতার শিয়ালদা রেলস্টেশন ছেড়ে ঢাকার ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে পা দিয়ে হতাশ না হয়ে উপায় ছিল না। আমার মেজ ভাইটি এখনও স্মরণ করে যে স্টেশনের অন্ধকার দেখে তার কান্না পেয়েছিল। সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতার উদ্দীপনা রেলস্টেশনের সামান্যতাকে ঢেকে দিতে পারেনি। স্টেশনের বাইরে এসে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করা, ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে অনিশ্চিত ঠিকানায় যাওয়া মোটেই আকর্ষণীয় ঘটনা ছিল না। আলাদা বাসা পাওয়া যায়নি, উঠতে হয়েছিল এক আত্মীয়ের বাসাতে। সেখানে বিদ্যুৎ ছিল টিম টিমে, পানি আনতে হতো রাস্তার কল থেকে। সুয়েরেজের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। বাইরে পাবলিক টান্সপোর্ট বলতে ছিল মুড়ির টিনের বাস। শুনেছি এমনই নিম্নমানের ছিল এই শহর যে প্রথমে যে ইংরেজ রাজকর্মচারীকে পূর্ববঙ্গের গভর্নর হতে অনুরোধ করা হয়েছিল, সরেজমিনে শহরের দশা দেখে ফিরে গিয়ে তিনি বলেছেন গভর্নর হওয়াতে তাঁর আগ্রহ নেই, ঢাকা শহর তাঁর কাছে বসবাসের জন্য উপযুক্ত ঠেকেনি। যে বাড়িতে থাকতে হবে সেটা মোটেই পছন্দ হয়নি, তদুপরি শুনেছেন শহরে মশার উৎপাত ভীষণ। এর পরে অবশ্য আরেকজন ইংরেজ এসেছিলেন গভর্নর হয়ে, কিন্তু বেশি দিন থাকেননি।
সাতচল্লিশের দেশভাগ উন্নতির বৈষম্যমূলক ধারাকেই সাহায্য করেছিল এগিয়ে যেতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অমিয় দাশগুপ্তের জন্য গবেষণার একটা জরুরি ক্ষেত্র ছিল মুদ্রাস্ফীতি ও কালোবাজারি। এরা উভয়েই পুঁজিবাদের অবিচ্ছেদ্য সহচর। দেশভাগ এই দুই সমস্যার সমাধান করেনি, উল্টো বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলা দখল করে নেয়, তার পর পরই বাংলায় ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। উপনিবেশিক ইংরেজ যখন তার শাসনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তখন, ১৯৪৩ সালে, বাংলায় আরেকটি দুর্ভিক্ষ ঘটে। পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে খ্যাত এই দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষ লোক মারা যায় বলে কথিত আছে। উভয় দুর্ভিক্ষই পুঁজিবাদী শাসনের দৌরাত্ম্যের অবদান। সাতচল্লিশের দেশভাগের পরে পূর্ববঙ্গে যে অবস্থা হয়েছিল তাকে প্রায়-দুর্ভিক্ষ বলাটা মোটেই অসঙ্গত নয়। ১৯৭১ সালে আমরা দ্বিতীয়বার স্বাধীন হলাম। এবারও, তিন বছর যেতে না যেতেই দুর্ভিক্ষ হলো, ১৯৭৪-এ। কোনো সন্দেহ নেই যে সমাজ এগুচ্ছে, শাসন-ক্ষমতা বিলক্ষণ হস্তান্তরিত হচ্ছে, কিন্তু সমাজ-বিকাশের ধারাটা সেই একই রয়ে গেছে। সেটি পুঁজিবাদী। উন্নতি অল্প মানুষের, অধিকাংশ মানুষের সুখশান্তিকে পদদলিত করে। স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়িয়েছে বড় রাষ্ট্রকে আয়তনে ছোট-করা এবং ছোট রাষ্ট্রের পরিসরে পুঁজিবাদকে বেপরোয়া ভাবে উন্নত হওয়ার জন্য সুযোগ করে দেওয়া। পুঁজিবাদ মুক্ত হয়েছে; কেবল মুক্ত নয়, এখন সে উন্মুক্তই।
বাংলার দারিদ্র্য সুপরিচিত। ইংরেজের আগমনের আগে অর্থনৈতিক ভাবে বাংলা ভালোভাবেই এগুচ্ছিল। সেই অগ্রগতির সুঘ্রাণই ইংরেজকে এখানে টেনে আনে। তারপর শুরু হয় লুণ্ঠন। এর আগে লুণ্ঠন করেছে মোগলরা। কিন্তু কাজটা ইংরেজ যেভাবে করেছে তা তুলনাবিহীন। তারা কেবল লুণ্ঠন করেনি, পাচার করেছে। স্থলে জলে এবং মাটির তলে যত সম্পদ ছিল খুঁজে খুঁজে বের করে নিঃস্ব করেছে বাংলাকে। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গ ছিল অধিক নিষ্পেষিত। বাংলার রাজধানী ছিল কলকাতায়, ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা, চাকরি-বাকরি সবকিছু সেখানেই। স্বাধীন হতে গিয়ে সেই পূর্ববঙ্গ খপ্পড়ে পড়ে গেল অবাঙালি শাসনের, তার অবস্থার বিশেষ উন্নতি হলো না; যেটুকু হলো সেটুকুও ওই পুঁজিবাদী চরিত্রের, যার পদে পদে বৈষম্য, পরতে পরতে শোষণ ও আর্তনাদ। একাত্তর সালে পূর্ববঙ্গ আবারও স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু দেশের মানুষ মুক্ত হতে পারেনি; ঝেড়ে ফেলতে পারেনি কাঁধের পুঁজিবাদী জোয়ালটাকে। উন্নতির অন্তরালে অবনতি রয়ে গেছে, দুঃশাসকের মতো।
যে-সময়টার কথা অলকনন্দা বলেছেন পূর্ববঙ্গের অনগ্রসরতা তখন নানাভাবেই উন্মোচিত। শিল্পকারখানা ছিটেফোঁটা কিছু ছিল, কিন্তু তা অর্থনীতিতে বড় কোনো পরিবর্তন আনেনি। অলকনন্দার মাতামহ উপেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন ইংরেজদের পাট কোম্পানির বড়বাবু। পাট কোম্পানি পাট কিনতো, পাটকলগুলো ছিল কলকাতায়, ছিল তারা বিলেতেও। পাটের ব্যবসাতে অর্থাগম হতো, নারায়ণগঞ্জে পাটের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিলেত থেকে লোক আসতো, ঔপন্যাসিক রুমার গডেন শীতলক্ষ্যা তীরে পারিবারিক বসবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে চমৎকার একটি উপন্যাস লিখেছেন, সেটি নিয়ে চলচ্চিত্রও হয়েছে; নারায়ণগঞ্জের পাট কোম্পানির কাজের সঙ্গে যুক্ত খান বাহাদুর ওসমান আলীও পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু পাট ব্যবসাতে ধস নেমেছিল ১৯২৯-এর বিশ্বমন্দার সময়ে। দাশগুপ্ত পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যে তখন চিড় ধরে। কিছুদিনের মধ্যে মাতামহ মারাই গেলেন।
এর পরে অলকনন্দার মামা সংসারের প্রধান হয়ে ওঠেন। তাঁর পেশা ছিল ওকালতি। আগেকার দিনে মধ্যবিত্তের জন্য বড় ভরসা সরকারি চাকরি। আর ছিল জামিদারি। বড় জমিদাররা কলকাতাতেই থাকতেন, ছোট জমিদাররাও সেখানে থাকাটাই পছন্দ করতেন। অন্য পেশার মধ্যে ছিল শিক্ষকতা ও চিকিৎসা। ছিল ছোটখাটো ব্যবসা। বড় ব্যবসা ইংরেজরাই করতো। এক সময়ে ছিল নীল, পরে এসেছে পাট। চামড়ার ব্যবসা ছিল; তবে সেটা অস্থানীয়দের দখলেই থাকতো। ঢাকার অবাঙালি নবাবরা চামড়ার ব্যবসা করেই ভাগ্য গড়েছিলেন। ওকালতিতে যাঁরা ভালো করতেন তাঁদের অবস্থা অবশ্য খারাপ ছিল না, আয়-রোজগার ভালোই ছিল। কিন্তু অধিকাংশ উকিলই ছিলেন ভালো না-করার দলে। অলকনন্দার মামা ছিলেন ভালো করার দলে। এই দীনহীন অবস্থাতেও অবশ্য চর্চা ছিল সংস্কৃতির। শিক্ষা, গান-বাজনা, নাটকের মঞ্চায়ন ছিল; চর্চা ছিল সাহিত্যেরও।
বড় বড় আঘাত এসেছে দুর্ভিক্ষে, দাঙ্গায়, এর পরবর্তীতে দেশভাগে। ১৯৪৩-এ দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গা এক সঙ্গে তৎপরতা চালিয়েছে। কলেজ (বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁরা কলেজ বলতেন) থেকে ফিরে এসে অমিয় দাশগুপ্ত একদিন বলেছিলেন কি ভাবে তিনি দেখলেন অনাহার-ক্লিষ্ট এক বৃদ্ধা রাস্তায় ওপরে মরে পড়ে গেলেন। ঠিক ওই সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই দাঙ্গা এসে হামলে পড়েছিল।
দাঙ্গার একটি ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণীয়। অলকনন্দা সেটি স্মরণ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্রীদের উদ্যোগে নাটকের আয়োজন করা হয়েছিল। ছাত্রীদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাই অধিক, অনুষ্ঠানের শুরুতে ‘বন্দেমাতরম’ গানটি গাওয়া হয়। আর তাতেই বাধে গোলমাল। মুসলমান ছাত্র ও ছাত্রীরা প্রতিবাদ জানায়; শুরু হয়ে যায় চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি। অলকনন্দার বয়স তখন মাত্র ছয়। বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ার অন্য শিশুদের সঙ্গে তিনিও এসে বসেছিলেন মঞ্চের সামনে, সতরঞ্জিতে। হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেলে তাঁর পিতার একজন মুসলমান ছাত্র অলকনন্দাকে নিরাপত্তা দেন, কোলে তুলে নিয়ে।
মারামারি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে কার্জন হল এলাকাতে। সভাগৃহের পাশেই ছিল পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক সত্যেন বসুর কামরা। সেই সন্ধ্যাতেও তিনি যথারীতি তাঁর গবেষণা কাজে মগ্ন। হৈ চৈ শুনে ছুটে বেরিয়ে এসে বিবদমান ছাত্রদের মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়ে যান। ‘করিস কি করিস কি’ বলে তাদের নিবৃত্ত করেন।
ঘটনা কিন্তু সেখানেই শেষ হয় নি। সংঘর্ষ দাঙ্গার রূপ নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরের দিন মারমুখী দুই সম্প্রদায়ের ছাত্রদেরকে থামাতে গিয়ে অর্থনীতির শেষ বর্ষের ছাত্র নাজির আহমদ ছুরিকাঘাতে আহত হন, পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। অলকনন্দার বইতে অবশ্য ওই হত্যাকা-ের উল্লেখ নেই। এটি ছিল তাঁর অভিজ্ঞতার এলাকার বাইরে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর অবশ্য দাঙ্গা এর পর আর হয়নি; কিন্তু শহরে হয়েছে। ঘটেছে অন্যত্রও। চূড়ান্ত দাঙ্গাটি ঘটে কলকাতাতে, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টে। তাতে হাজার দশেক লোক নিহত হয়। এবং এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে দেশভাগ ছাড়া ক্ষমতা ভাগাভাগির অন্য কোনো উপায় নেই।
ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়